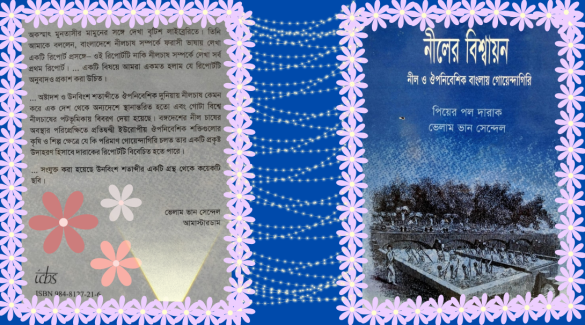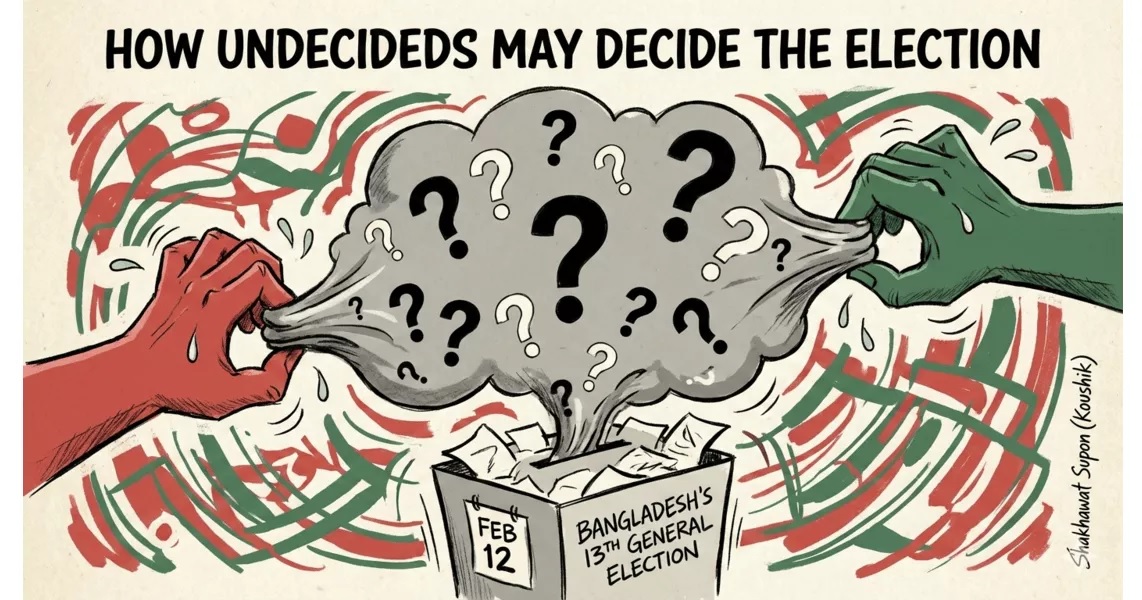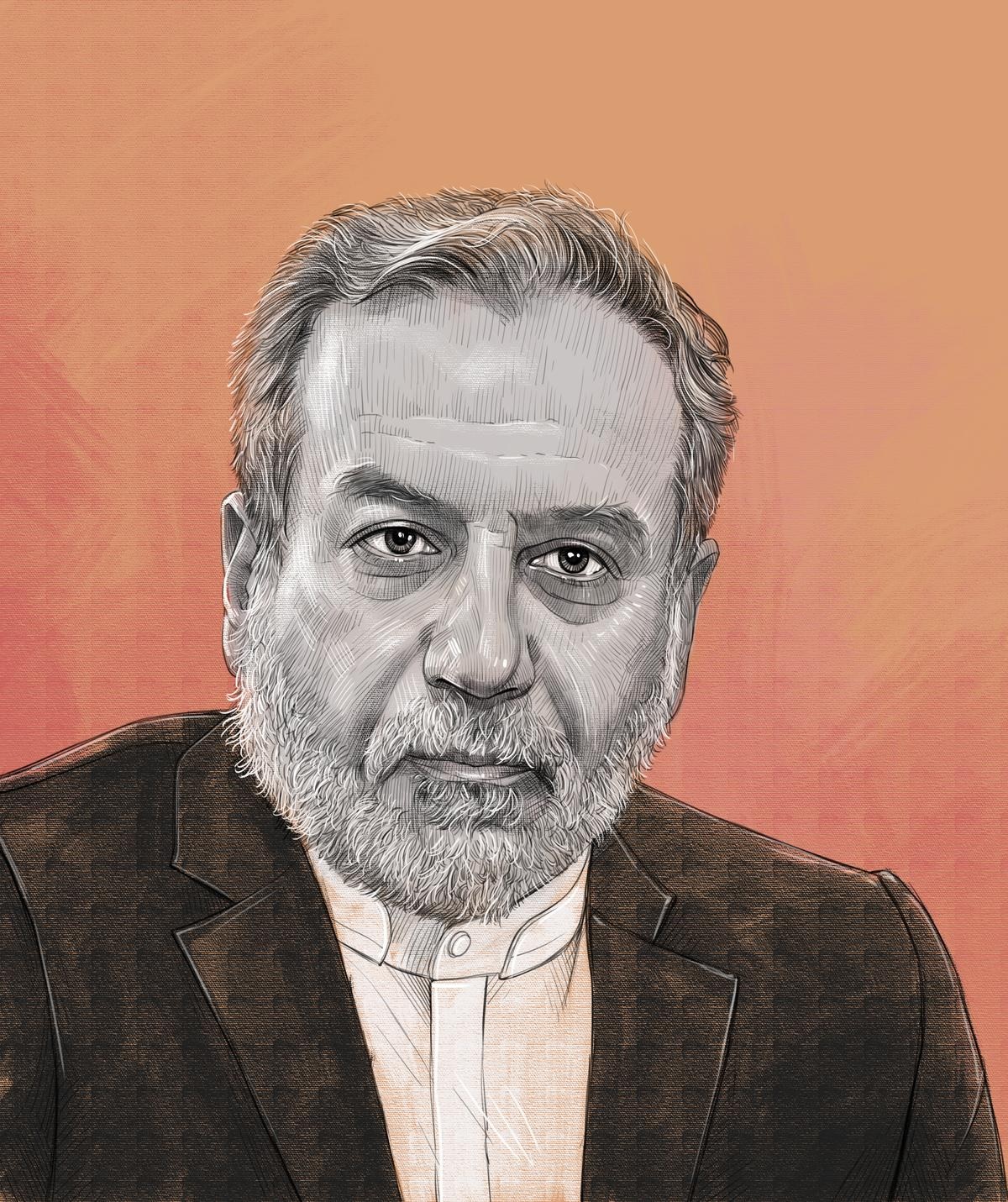পিয়ের পল দারাক ও ভেলাম ভান সেন্দেল
অনুবাদ : ফওজুল করিম
১৮৩৭ সালের জনৈক পর্যবেক্ষকের অভিমত অনুযায়ী ভারতের প্রধান রফতানী দ্রব্যই ছিল নীল। ভারতের অন্যান্য স্থানেও নীল প্রস্তুতের ক্যারেবীয় পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। এমনকি দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও তাই। অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত নীলের সঙ্গে বাংলাদেশের নীলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না।
“বিহার ও বঙ্গে প্রস্তুত নীল মান ও পরিমাণে অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত নীলের চেয়ে ছিল উৎকৃষ্টতর। উর্বর মাটি ও গ্রীষ্ম প্রধান জলবায়ু নীলের জন্য উপযোগী ছিল বলে মনে হয়। উৎপাদনকারীদের অদক্ষতা কিংবা মাটি ও জলবায়ুর অনুপযোগিতা অথবা এই সবগুলো কারণের জন্যেই হোক না কেন ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে যে নীল উৎপন্ন হত তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।**
উরন্ত কিছু সহায়তাদান ও ব্যবস্থা গ্রহণের পরও বিশ্বে বাংলাদেশকে নীল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে করা হত কঠোর সংগ্রাম। প্রথম পর্যায়ের উলোভাদের প্রায় সব প্রচেষ্টা হল ব্যর্থ। তারা দোষ দিল প্রতিকূল বাণিজ্যের উপর। উদ্যোক্তাদের লা যানবাহনের দীর্ঘ সারির উপর ও বাজার সম্পর্কে হালের তথ্য না স্বাস্ত্যার উপর। বাংলার এক বিশিষ্ট নীল ব্যবসায়ী ১৭৯০ সালে এই বলে অভিযোগ সারমারয় বাংলাদেশের নীলকরদের চাইতে দ্বিগুণ সুবিধা নিয়ে বাজারে (লন্ডন) যান ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ব্যবসায়ীরা।”
উইচিরবদের ছিল সরবরাহের সমস্যা। কোনো জমিতে নীলকুঠি করতে হলে সরকারের কাছে থেকে অনুমতি নিতে হত। প্রথম দিকে ২৫ হেক্টরের বেশি জমি বরাদ্দ করা হত। (প্রায় ৭৫ বিঘা) জমির স্বল্পতার কারণে নীলকররা তার পাশের কৃষকদের নীল উৎপাদনের জন্য বলপ্রয়োগ করত। এভাবে প্রতিবেশী কৃষকদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হত। এতে জড়িয়ে পড়ত জমিদাররাও।
আবার জমি কেন্দ্র করে কিংবা নীলের সরবরাহ কেন্দ্র করে হাতাহাতি শুরু হত নীলকরদের নিজেদের মধ্যেও প্রথম দিকে বাংলার নীলের মান আশানুরূপ ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বাংলার নীলের এতই সুনাম হয় যে বলা হত এই নীল উৎকৃষ্টতার দিক থেকে আমেরিকান ও ফরাসী নীলকে ছাড়িয়ে গেছে।

 Sarakhon Report
Sarakhon Report