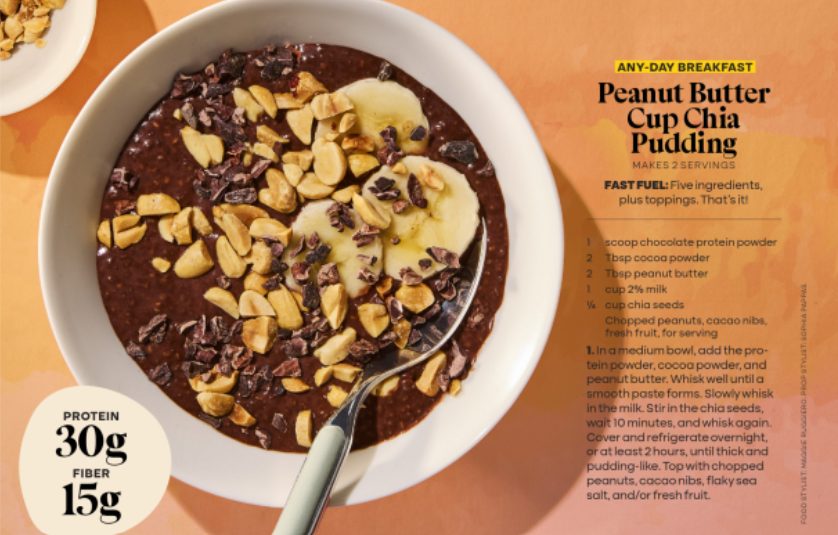আমি যখন নয় বছর বয়সী, তখন নেলসন ম্যান্ডেলাকে রবেন দ্বীপের কারাগারে পাঠানো হয়। ছোটবেলায় স্কুলে তাঁর কথা শিখেছি, আর সন্ধ্যার সংবাদে বারবার দেখেছি বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের খবর। দশক পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার এবং একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই। সরাসরি দেখা হলে তিনি কল্পনার চেয়েও বেশি প্রেরণাদায়ক মনে হয়েছিলেন। তাঁর বিনয় ও সাহস আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে, যা আমি কখনো ভুলব না।
তাই প্রিটোরিয়ায় নেলসন ম্যান্ডেলা বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পাওয়া ছিল আমার জন্য বিশেষ এক সম্মান। আমি আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করি এবং দ্রুত আমার বক্তব্য প্রস্তুত করতে বসি।
আমি আফ্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আশাবাদ শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—কেন আমি মনে করি পরবর্তী এক প্রজন্মে এই মহাদেশ অন্য যেকোনো মহাদেশের চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন আনতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে।
কারণ আফ্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ মহাদেশ, আর তারুণ্য প্রায়ই এক বিশেষ গতিশীলতার সঙ্গে আসে। আমি যখন বিশ বছরের, তখন পল অ্যালেনের সঙ্গে আমরা মাইক্রোসফট শুরু করি। জোহানেসবার্গ, লাগোস ও নাইরোবির স্টার্টআপ বুমে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারাও ততটাই তরুণ; তারা যে হাজারো ব্যবসা তৈরি করছেন, সেগুলো ইতিমধ্যেই মহাদেশজুড়ে মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্সে ডিজিটাল বিপ্লব যত এগোবে, এই সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

তবে আফ্রিকা জুড়ে ইতিবাচক পরিবর্তন নিজে নিজে হবে না। প্রকৃত ফল আসবে তখনই, যখন আফ্রিকানরা মহাদেশজুড়ে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার সবার মধ্যে এই উদ্ভাবনী প্রতিভাকে মুক্ত করে দিতে পারবেন। তা নির্ভর করছে—তরুণদের সবাইকে উন্নতির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কি না—এই প্রশ্নের জবাবের ওপর।
এই প্রশ্ন এখনো খোলা—এবং সেটাই আমার বক্তব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়, যা আমি আজ প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি। এই বক্তৃতা দিতে পারা আমার জন্য সম্মানের, এবং আমন্ত্রণের জন্য নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। নিচে ভিডিওর পর আমার পুরো বক্তব্য পড়তে পারবেন।
প্রদত্ত বক্তব্য
নেলসন ম্যান্ডেলা বার্ষিক বক্তৃতা
প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা
১৭ জুলাই ২০১৬
বিল গেটস:
ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা, মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রলোকগণ। গ্রাসা মাশেল, প্রফেসর ন্দেবেলে, ভাইস চ্যান্সেলর ডে লা রে, মামেলোদি এলাকার পরিবারসমূহ, বন্ধু ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
নেলসন ম্যান্ডেলার নামে নামাঙ্কিত বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আমি ভাবতে পারি না।
এ বছর বক্তৃতার থিম ‘একসঙ্গে বসবাস’—এতে আমি ভীষণ উৎফুল্ল।
এটি সত্যিই যথাযথ, কারণ নানা দিক থেকে দেখলে ‘একসঙ্গে বসবাস’ই ছিল নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনেরও প্রধান থিম।
তিনি যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়েছেন, তা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার উপর—মানুষকে আলাদা করে রাখা, আমাদের উপরিতলীয় পার্থক্যগুলোকে আমাদের সাধারণ মানবিকতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা।
আজও দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ পূর্ণ অর্থে ‘একসঙ্গে বসবাস’-এর জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু আপনারা সেই আদর্শের অনেক কাছাকাছি, কারণ নেলসন ম্যান্ডেলা ও আরও অনেকে এক ও অভিন্ন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন।
আমি যখন মাত্র নয় বছর বয়সে, তখন নেলসন ম্যান্ডেলাকে রবেন দ্বীপে পাঠানো হয়। স্কুলে তাঁর কথা শিখেছিলাম। সন্ধ্যার খবরে নিয়মিত বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের রিপোর্ট দেখার কথা মনে আছে।

১৯৯৪ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচনের অর্থায়নে সহায়তার জন্য আমাকে ফোন করেন, তখন প্রথমবার তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়।
আমি তখন মাইক্রোসফট পরিচালনা করছিলাম—বেশিরভাগ সময় সফটওয়্যারেই ডুবে থাকতাম। কিন্তু তাঁকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম, আর জানতাম সেই নির্বাচন ছিল ইতিহাস-গঠনকারী। তাই যতটা পেরেছি, সাহায্য করেছি।
আফ্রিকায় আমার প্রথম সফর তারও এক বছর আগে—১৯৯৩ সালে—যখন আমি আর আমার স্ত্রী মেলিন্ডা পূর্ব আফ্রিকায় গিয়েছিলাম।
প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অপূর্ব, মানুষ আন্তরিক, কিন্তু সেখানে যে দারিদ্র্য আমরা প্রথমবার এত কাছ থেকে দেখলাম, তা আমাদের অস্থির করে তোলে—একই সঙ্গে উদ্দীপিতও করে।
অবশ্যই আমরা জানতাম আফ্রিকার কিছু অংশ দরিদ্র। কিন্তু মহাদেশে গিয়ে এই বিষয়টি একটি বিমূর্ত ধারণা থেকে এমন এক অবিচারে রূপ নিল, যাকে আর উপেক্ষা করা যায় না।
আমরা সবসময়ই জানতাম, একসময় আমাদের সম্পদ দাতব্যে দেব। কিন্তু এত প্রকট বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে আমরা ভাবতে শুরু করলাম—কীভাবে আরও তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা যায়।
এই তাগিদ আরও বেড়ে যায় ১৯৭৭ সালের আরেক সফরে, যখন আমি মাইক্রোসফটের প্রতিনিধিরূপে প্রথমবার জোহানেসবার্গে আসি।
শহরের সমৃদ্ধ অংশে ব্যবসায়িক বৈঠকেই বেশিরভাগ সময় কেটেছে, কিন্তু সোয়েতোর একটি কমিউনিটি সেন্টারেও গিয়েছিলাম, যেখানে মাইক্রোসফট কম্পিউটার দান করছিল।
তখনকার সোয়েতো এখনকার থেকে বেশ আলাদা ছিল। এই সফর আমাকে শেখায়—আমি সারা জীবন যে আরামের বুদবুদের মধ্যে ছিলাম, তার বাইরে পৃথিবী সম্পর্কে জানার কত কিছু বাকি।
কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকেই দেখি, কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। যে কম্পিউটারটি আমি দান করছিলাম, সেটি চালু রাখতে বাইরে একটি ডিজেল জেনারেটরের সঙ্গে এক্সটেনশন কর্ড জুড়ে রাখা হয়েছে। বুঝলাম, আমি বেরিয়ে যেতেই জেনারেটরটি আরও জরুরি কোনো কাজে সরিয়ে নেওয়া হবে।
তখন প্রযুক্তিখাতের ফাঁক-ফোকর নিয়ে প্রস্তুত করা বক্তব্য পড়তে পড়তেই বুঝলাম—এটি গল্পের খুব সামান্য অংশ। কম্পিউটার মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সাহায্য করতে পারে, মহাদেশের জীবনে বিপ্লব আনতেও তাদের ভূমিকা আছে। কিন্তু কম্পিউটার একা রোগের বিরুদ্ধে লড়তে বা শিশুদের সুস্থ করতে পারে না। আর যদি সেগুলো চালু করার মতো বিদ্যুৎই না থাকে, তবে তাদের দিয়ে তো কিছুই সম্ভব নয়।

তারপরই মেলিন্ডা আর আমি আমাদের ফাউন্ডেশন শুরু করি—কারণ অপেক্ষার মূল্য যে কত চড়া, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।
আমাদের কাজের ভিত্তি খুব সরল—যে-ই হোক, যেখানে-ই থাকুক, প্রত্যেকে যেন সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনের সুযোগ পায়।
গত পনের বছর আমরা সমস্যা সম্পর্কে শিখেছি, আর এমন ‘লিভারেজ পয়েন্ট’ খুঁজেছি, যেখানে কাজ করলে মানুষের সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বাড়ে।
ফাউন্ডেশনের কাজে নিয়মিত আফ্রিকায় আসা শুরু করার পরই নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় হয়। এইডস ছিল আমাদের ফাউন্ডেশনের প্রথম দিকের কাজগুলোর একটি; এ বিষয়ে তিনি ছিলেন উপদেষ্টা ও প্রেরণার উৎস।
আমরা একটি বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলেছি—এইচআইভি/এইডসকে ঘিরে সামাজিক কলঙ্ক। তাই ২০০৫ সালটি আমি স্পষ্ট মনে করি—যখন তাঁর নিজের ছেলে এইডসে মারা যান। ছেলের মৃত্যুর কারণ গোপন না করে তিনি তা প্রকাশ্যে জানালেন—কারণ তিনি জানতেন, রোগ ঠেকাতে হলে ভয় ও লজ্জার দেয়াল ভাঙতেই হবে।
নেলসন ম্যান্ডেলার উত্তরাধিকার স্মরণ করা জরুরি—এ সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।
কিন্তু ম্যান্ডেলার মন ছিল ভবিষ্যতমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন—মানুষ ভবিষ্যৎকে অতীতের চেয়ে ভালো করতে পারে। তাই বাকিটা আমি ভবিষ্যৎ নিয়েই বলব।
দক্ষিণ আফ্রিকা কী হতে পারে? আফ্রিকা কী হতে পারে? পৃথিবীই বা কী হতে পারে? আর তা করতে আমাদের কী করতে হবে?
দুই হাজার সালে জাতিসংঘের গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এমন এক ভিত্তি তৈরি করেছিল, যার ওপর দাঁড়িয়ে—আফ্রিকাসহ—গত পনের বছরে বিশ্ব অসাধারণ অগ্রগতি করেছে।
আর সদ্য ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নত পৃথিবী গড়ার আরও উচ্চাভিলাষী টার্গেট নির্ধারণ করেছে।
অগ্রগতির কথা বললে আমি সবসময় শিশুদের বেঁচে থাকার হার দিয়ে শুরু করি—কারণ শিশু বাঁচছে না মরছে, এটি কোনো সমাজের মূল্যবোধের সবচেয়ে মৌলিক নির্দেশক।

১৯৯০ সাল থেকে সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশু মৃত্যুর হার ৫৪ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ, ২৫ বছর আগের তুলনায় প্রতিবছর প্রায় দশ লাখ কম শিশু মারা যাচ্ছে।
আফ্রিকার দশটি দেশ শিশু মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশ কমানোর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।
একই সময়ে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির হার কমেছে। আর যদিও গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর, তবু এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আফ্রিকার বহু দেশে প্রবৃদ্ধি ছিল দৃঢ়।
এ অগ্রগতি বাস্তব—কিন্তু ‘আফ্রিকা রাইজিং’ কথাটাই মহাদেশের জীবনযাপনের পুরো গল্প বলে না।
প্রথমত, অগ্রগতি হয়েছে অসমভাবে—দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনারা নিজেই তা জানেন।
গত বছরের নেলসন ম্যান্ডেলা বক্তৃতায় ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি দেখিয়েছিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় আয় বৈষম্য, উদ্ধৃত করছি, ‘পৃথিবীর প্রায় যেকোনো জায়গার চেয়েও বেশি।’
সাধারণভাবে, অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় আফ্রিকার দেশগুলোতে বৈষম্যের হার বেশি—এবং অঞ্চলে গড় দেশজ উৎপাদন বাড়লেও বহু দেশ তাতে সমানভাবে অংশ নিতে পারেনি। বৈষম্য আছে দেশের মধ্যে এবং দেশগুলোর মধ্যেও।
তাই অগ্রগতি যতক্ষণ না সবার, সর্বত্র, ততক্ষণ ‘একসঙ্গে বসবাস’-এর সত্যিকারের প্রতিশ্রুতি অধরাই থাকবে।
দ্বিতীয়ত, আফ্রিকা বড় অগ্রগতি করলেও বেশিরভাগ সূচকে এখনও বিশ্বের পেছনে। সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতি বারোটি শিশুর মধ্যে একটি পাঁচ বছর পূর্ণ করার আগেই মারা যায়। ২৫ বছর আগের তুলনায় এটি বিরাট উন্নতি, তবু আফ্রিকান শিশুরা এখনও বিশ্বগড়ের তুলনায় বারো গুণ বেশি মৃত্যুঝুঁকিতে।
আর দারিদ্র্য ও অপুষ্টির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিতে কমছে না—ফলে ১৯৯০ সালের তুলনায় আজ দরিদ্র ও অপুষ্ট মানুষের মোট সংখ্যাও বেড়েছে।
তৃতীয়ত, এই অগ্রগতি ভঙ্গুর। মহাদেশের দুই বৃহৎ অর্থনীতি—দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাইজেরিয়া—গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে। নতুন হুমকিরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে—ইবোলার সংকট বহু জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা স্পষ্ট করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যেই বহু দেশের চাষিদের ওপর পড়ছে।
সংক্ষেপে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে হলে—আফ্রিকাকে আরও বেশি, আরও দ্রুত করতে হবে—এবং সবার কাছে তার সুফল পৌঁছাতে হবে। কঠিন—তবু আমি বিশ্বাস করি, সম্ভব।
গত পনের বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা আমাদের সামনে উদাহরণ ও শিক্ষা রেখেছে। বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি উন্নয়ন-চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমাধানের পরিসর বাড়িয়ে দিয়েছে। আর আছে আফ্রিকার মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি।
নেলসন ম্যান্ডেলা বারবার একটি বিষয় বলেছেন—তারুণ্যের শক্তি। তিনি জানতেন—কারণ তিনি নিজেও কুড়ির কোঠায় থাকতেই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যুব শাখায় কাজ শুরু করেছিলেন।
পরে তিনি বোঝেন—তরুণদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টি তুলে ধরা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে অত্যন্ত কার্যকর। ‘তরুণরা সুযোগ পাওয়ার যোগ্য’—এই বিশ্বাস সর্বজনীন আবেদন রাখে।
তরুণদের ব্যাপারে ম্যান্ডেলার সঙ্গে আমি একমত—এ কারণেই আমি এই মহাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। জনতাত্ত্বিকভাবে আফ্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ মহাদেশ—তারুণ্য এক বিশেষ গতিশীলতার উৎস হতে পারে।
আগামী পঁয়ত্রিশ বছরে আফ্রিকায় দুইশ’ কোটিরও বেশি শিশু জন্মাবে। ২০৫০ সালে বিশ্বের মোট শিশুদের চল্লিশ শতাংশই থাকবে এই মহাদেশে।
অর্থনীতিবিদরা ‘জনমিতিক লভ্যাংশের’ কথা বলেন—যখন কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা নির্ভরশীলদের তুলনায় বেশি হয়, তখন অসাধারণ প্রবৃদ্ধি সম্ভব। সত্তরের-আশির দশকে পূর্ব এশিয়ার দ্রুত প্রবৃদ্ধির পেছনে তরুণদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ বড় কারণ ছিল।
তবু আমার কাছে তরুণদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক—তাদের চিন্তার ধরন। তরুণরা উদ্ভাবনে বয়স্কদের চেয়ে এগিয়ে—কারণ তারা অতীতের সীমাবদ্ধতায় বন্দি নয়।
আমি উনিশ বছর বয়সে মাইক্রোসফট শুরু করি—তখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটিও তরুণ। আমরা পুরোনো ধারণার কাছে বাঁধা ছিলাম না—কম্পিউটার কী করতে পারে বা করা উচিত—এসব নিয়েও না। আমরা পরবর্তী বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখতাম—পৃথিবীজুড়ে ঘুরে বেড়াতাম সেসব আইডিয়া ও টুলের খোঁজে, যা আমাদের তা বানাতে সাহায্য করবে।
শুধু মাইক্রোসফটই নয়—স্টিভ জবস একুশ বছর বয়সে অ্যাপল শুরু করেন; মার্ক জাকারবার্গ উনিশ বছর বয়সে ফেসবুক।
আফ্রিকার ‘সিলিকন সাভান্না’—জোহানেসবার্গ ও কেপটাউন থেকে লাগোস ও নাইরোবি—এ স্টার্টআপ বুমে নেতৃত্বদানকারী উদ্যোক্তারা বয়সে যেমন তরুণ, দৃষ্টিভঙ্গিতেও তেমন। তারা যে হাজারো ব্যবসা তৈরি করছেন, তা ইতিমধ্যেই মহাদেশজুড়ে দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আনছে।
কয়েক দিনের মধ্যে আমি এ ধরনের কিছু তরুণ উদ্ভাবকের সঙ্গে দেখা করব—যেমন, কেনিয়ার একুশ বছরের এক তরুণ যিনি দেশের প্রথম সফটওয়্যার কোডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন—যাতে অন্য তরুণরা প্রোগ্রামিং শেখে। কিংবা এখানকারই তেইশ বছরের এক সামাজিক উদ্যোক্তা—পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ দিয়ে স্কুলব্যাগ বানান; ব্যাগগুলো দূর থেকে দৃশ্যমান—শিশুরা স্কুলে যেতে-আসতে নিরাপদ থাকে—এবং তাতে ছোট সৌর প্যানেল থাকে, যা পথেই চার্জ হয়ে বাড়িতে পড়াশোনার জন্য আলো দেয়।

এই প্রতিভার পূর্ণ লভ্যাংশ পেতে হলে—আফ্রিকার বাড়তে থাকা তরুণ জনসংখ্যার সবাইকে—হ্যাঁ, সবাইকে—উন্নতির সুযোগ দিতে হবে।
নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, “দারিদ্র্য স্বাভাবিক নয়—এটি মানুষের তৈরি—এবং মানুষের কর্মেই তা দূর করা সম্ভব।”
আমরাই সেই মানুষ—আমাদেরই কাজ করতে হবে—এবং এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কারণ এই অনন্য মুহূর্ত স্থায়ী নয়। তরুণদের পথের বাধা সরাতে হবে—যাতে তারা নিজেদের সম্ভাবনা ধরতে পারে।
তরুণরা যদি অসুস্থ ও অপুষ্ট হয়, তাদের দেহ-মন পূর্ণ বিকশিত হবে না। তারা যদি ভালো শিক্ষা না পায়, তাদের মেধা সুপ্তই থেকে যাবে। অর্থনৈতিক সুযোগ না পেলে তারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না।
কিন্তু আমরা যদি সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করি—যদি নিশ্চিত করি আফ্রিকার তরুণদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে—তবে তারা ভবিষ্যৎ বদলানোর জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, জ্ঞানীয় ও মানসিক সম্পদ পাবে। এই মহাদেশে উন্নতি হবে ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত। ‘একসঙ্গে বসবাস’-এর প্রকৃত অর্থ—নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি—বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে দেবে।
পনের বছর আগে মেলিন্ডা আর আমি ফাউন্ডেশন শুরু করার সময় নিজেদের জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোথায় কাজ করলে প্রভাব সবচেয়ে বেশি? দ্রুতই বোঝা গেল—স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ শীর্ষ অগ্রাধিকার। মানুষ সুস্থ না থাকলে জীবনের অন্য কিছুর দিকে মন দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বাস্থ্য যত উন্নত হয়, জীবনের প্রতিটি সূচকই উন্নত হয়।
গত পনের বছরে আমাদের ফাউন্ডেশন আফ্রিকায় নয় বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে। আর আমরা এ বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব।
আগামী পাঁচ বছরে আমরা আরও পাঁচ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করব।
এই অর্থের একটি অংশ সংক্রামক রোগ ঠেকাতে নতুন ও উন্নত টিকা ও ওষুধ আবিষ্কার ও উন্নয়নে গেছে। আমরা বৈশ্বিক অংশীদারিত্বেও বিনিয়োগ করেছি—যারা মহাদেশজুড়ে দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এসব সমাধান সেই মানুষদের কাছে পৌঁছে দেয়, যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
অসাধারণ অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে—একসঙ্গে আমরা অবিশ্বাস্য অগ্রগতি দেখেছি।
উদাহরণস্বরূপ, পুরো আফ্রিকা মহাদেশ দুই বছর ধরে পোলিওমুক্ত—এতে আমরা মানবজাতির কাছ থেকে চিরতরে পোলিও মুছে ফেলার নাগালের মধ্যে চলে এসেছি।
নবীনতম টিকাগুলো—যা শিশুদের দুইটি ধ্বংসাত্মক রোগ—নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া—থেকে সুরক্ষা দেয়—আজ আফ্রিকাজুড়ে শিশুদের কাছে পৌঁছাচ্ছে—যেমনটি ধনী দেশগুলোর শিশুদের কাছেও পৌঁছায়।
যেসব দেশ সম্প্রদায়ভিত্তিক শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছে—যেমন মালাউই, ইথিওপিয়া, রুয়ান্ডা—তারা শিশু মৃত্যুহার কমাতে বড় অগ্রগতি করেছে।
ম্যালারিয়া সংক্রমণ ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে—উন্নত চিকিৎসা ও প্রতিরোধের সরঞ্জামের কারণে।
আর পশ্চিম আফ্রিকায় উয়াগাদুগু পার্টনারশিপের মতো উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ নারীর কাছে গর্ভনিরোধক পৌঁছে দিচ্ছে—যা তাদের পরিবারের যত্ন নিতে সহজ করেছে।
এইচআইভি/এইডসেও ভালো অগ্রগতি হয়েছে—যদিও গল্পটি জটিল—এবং সামনে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ আছে।
কয়েক দিনের মধ্যে আমি ডারবানে আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনে কথা বলব। ২০০০ সালে যখন এই বৈশ্বিক সম্প্রদায় শেষবার সেখানে মিলিত হয়েছিল, তখন আফ্রিকায় মাত্র কয়েক হাজার মানুষ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিৎসা পেতেন। আজ আফ্রিকায় বারো মিলিয়নেরও বেশি মানুষ চিকিৎসাধীন—যাদের চতুর্থাংশেরও বেশি দক্ষিণ আফ্রিকায়।
এটি বিশাল সাফল্য—লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো গেছে। কিন্তু নতুন সংক্রমণের হার এখনও বেশি। সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন চব্বিশ বছরের কম বয়সী দুই হাজারেরও বেশি তরুণ নতুন করে সংক্রমিত হচ্ছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় তরুণদের এইচআইভি-জনিত মৃত্যু চার গুণ বেড়েছে।
আমাদের মানুষকে পরীক্ষা করাতে উৎসাহিত করতে হবে, চিকিৎসা নিতে আনতে হবে, আর যারা চিকিৎসাধীন, তাদের নিয়মিত ও সম্পূর্ণ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।
এইচআইভির পাশাপাশি যক্ষ্মাও উচ্চহারে রয়েছে—দক্ষিণ আফ্রিকাতেও—যেখানে টিবি/এইচআইভি সহ-সংক্রমণ এখনও ভয়াবহ।
তাই পরীক্ষা ও চিকিৎসা সহজলভ্য ও সুবিধাজনক করতে আরও সৃজনশীল পথ দরকার।
বিদ্যমান প্রতিরোধ পদ্ধতি—কনডম, স্বেচ্ছামূলক পুরুষ খতনা, মুখে খাওয়া প্রতিরোধক ওষুধ—এসবের ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে।
আমাদের আরও নতুন ও উন্নত প্রতিরোধী সমাধানও উদ্ভাবন করতে হবে—যেমন মাসে একবার খেতে হয় এমন ওষুধ—অথবা কার্যকর ভ্যাকসিন।
আজকের চিকিৎসা জোরদারের পাশাপাশি এসব নতুন টুল উদ্ভাবনে কাজ না করলে—গত পনের বছরের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সাফল্য উল্টো পথে যেতে পারে। জনসংখ্যা বাড়ার কারণে, কেবল ‘যা করছি তাই’ যথেষ্ট হবে না—আরও বেশি করতে হবে।

পুষ্টি আফ্রিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। মহাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে—তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়—শারীরিক ও মানসিক সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আরও লক্ষ লক্ষ শিশু ক্ষুদ্র পুষ্টি-ঘাটতিতে ভোগে। এ প্রভাব সারাজীবন স্থায়ী হয়—পুরো প্রজন্মকে প্রভাবিত করে।
আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সভাপতি আকিন আদেশিনা ঠিকই বলেছেন—আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় অবদান ‘ধূসর অবকাঠামো’—অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্কশক্তি। সেই অবকাঠামো গড়ার শ্রেষ্ঠ উপায়—সঠিক পুষ্টি।
অপুষ্টি না কমালে সম্ভাবনার সর্বোচ্চটা অর্জন করা যাবে না।
আমরা জানি—মা ও নবজাতক ভালো পুষ্টি পেলে—স্তন্যপান তার মূল অংশ—শিশুর জন্য কিছু ভিটামিন-খনিজ অপরিহার্য।
পুষ্টি উন্নত করতে নানা পথ আছে—যেমন ফোর্টিফায়েড রান্নার তেল; ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ চিনি; আয়রন, জিংক, ভিটামিন ‘বি’ যুক্ত চিনি ও আটা।
সবচেয়ে উত্তেজনাকর অগ্রগতি—ফসলের জাত উন্নয়ন করে তাদের স্বাভাবিকভাবেই বেশি পুষ্টিকর করা। যেমন—কিশোর-কিশোরীরা উচ্চ-আয়রন সমৃদ্ধ বাজরা খেলে আয়রন ঘাটতির ঝুঁকি ছয় গুণ কমে। আর অর্ধেক কাপ বায়োফর্টিফায়েড কমলা-রঙা মিষ্টি আলু একটি শিশুর দৈনিক ভিটামিন ‘এ’-এর চাহিদা পূরণ করতে পারে।
ক্ষুদ্র পুষ্টির ঘাটতির খেসারত বিপুল—কিন্তু তা মোকাবিলার খরচ তেমন নয়।
নাইজেরিয়া ও উগান্ডার সাম্প্রতিক হিসাব বলছে—বামনত্ব (স্টান্টিং) কমাতে প্রতি এক ডলার বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সতেরো ডলার সমমূল্যের আয় বাড়ায়।
শিশুর দেহ-মন সুস্থ হলে পরের ধাপ—এমন শিক্ষা, যা তাদের সমাজের উৎপাদনশীল নাগরিক হতে জ্ঞান-দক্ষতা দেয়।
শিক্ষা উন্নত করা কঠিন—ফাউন্ডেশনের কাজের মাধ্যমে আমি নিজেও দেখেছি—আমেরিকায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় শিখনফল উন্নত করা সহজ নয়।
কিন্তু এই কঠিন কাজের গুরুত্ব অপরিসীম—ভালো শিক্ষা এমন এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা প্রতিটি তরুণকে সম্ভাবনার সর্বোচ্চটা অর্জনের সুযোগ দেয়।
আফ্রিকায়ও, আমেরিকার মতোই—ভালো শিক্ষার প্রাপ্যতা সবার জন্য নিশ্চিত করতে নতুন ভাবনা ও নতুন শিক্ষাপ্রযুক্তি দরকার।
উগান্ডায় ‘এডুকেট!’ নামে একটি সংস্থার তরুণ উদ্ভাবকেরা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে শেখাচ্ছেন—যাতে তারা নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে পারে।
আফ্রিকায় মোবাইল ফোনের ব্যাপকতা বিবেচনায়—ইন্টারনেট-সংযুক্ত মোবাইলভিত্তিক প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক দক্ষতা গঠনে সাহায্য করতে পারে—শিক্ষকদেরও ভালো ফিডব্যাক ও সহায়তা দেয়।
বিশ্বব্যাপী এডটেক খাত দ্রুত উদ্ভাবন করছে—নতুন মডেল ও সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে—যারা বিদ্যমান ব্যবস্থার বাইরে থাকা শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শুধু প্রবেশাধিকার বাড়ালেই হবে না—উচ্চমানের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও দরকার—যেখান থেকে আগামী প্রজন্মের বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও রাষ্ট্রনেতা গড়ে উঠবে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকার সেরা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে—আজ আমরা যেটিতে আছি, সেটিও তাদের একটি।
ফাউন্ডেশনের কাজ—স্বাস্থ্য ও কৃষি গবেষণায়—আমরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করি। মান বজায় রেখে আরও বেশি শিক্ষার্থীর জন্য প্রবেশাধিকার বাড়ানো সহজ নয়—তবু দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যতের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অঞ্চলের অন্যান্য দেশও দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে—যত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সর্বোচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিশ্চিত করলে ভালো হবে।
সুস্থ, শিক্ষিত তরুণরা পৃথিবীতে নিজেদের পথ করে নিতে মুখিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের শক্তিকে অগ্রগতির ধারায় আনতে অর্থনৈতিক সুযোগ দরকার।
এদের অনেকে কৃষিখাতে কাজ করবে—যেখানে এখনও অর্ধেকের বেশি কর্মশক্তি নিয়োজিত।
কৃষিতে উৎপাদনশীলতা অনেক বাড়াতে হবে। আজ যে বীজ ব্যবহার হয় তা কম ফলনশীল; মাটির গুণাগুণ ভালো নয়—ফলে অনেক কৃষক কেবল নিজেদের পরিবার চালানোর মতোই ফলাতে পারেন।
জলবায়ু পরিবর্তনে আবহাওয়া আরও চরম হলে—পুরোনোভাবে চললে চলবে না।
সমাধান—চেইনের প্রতিটি ধাপে ধারাবাহিক উদ্ভাবন—ক্ষেত থেকে বাজার পর্যন্ত।
প্রথমে—কৃষকের দরকার এমন সরঞ্জাম, যা দুর্যোগ ঠেকিয়ে উদ্বৃত্ত ফলাতে সাহায্য করবে—যেমন খরা, বন্যা, পোকার আক্রমণ ও রোগ-সহনশীল বীজ; মাটির পুষ্টি ফিরিয়ে আনতে সঠিক মিশ্রণের সাশ্রয়ী সার; সহজে দেওয়া যায় এমন গবাদিপ্রাণীর টিকা—যা পশুপালকে মহামারি থেকে রক্ষা করবে।
পরের ধাপে—কৃষকের দরকার বাজারের সঙ্গে সংযোগ—যেখানে ভালো দামে উপকরণ কিনতে পারে, উদ্বৃত্ত বিক্রি করতে পারে—লাভ করে পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি খামারেও বিনিয়োগ করতে পারে।
এভাবে কৃষকের সমৃদ্ধি বাড়লে খামার ও খামারের বাইরে নতুন কর্মসংস্থান হবে—বীজ বিক্রেতা, ট্রাকিং, প্রসেসিং প্ল্যান্ট—এমন নানা কৃষি-বাণিজ্য গড়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক এক বৈঠকে আমি কয়েকজন তরুণ ফসল প্রজননবিদের সঙ্গে দেখা করি—ইথিওপিয়া, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, উগান্ডা থেকে। উদ্ভিদের ফলনশীলতার বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। কাসাভা নিয়ে তাদের দক্ষতা দেখে আমি মুগ্ধ—আফ্রিকার বহু খাদ্যতালিকায় কাসাভা এক-তৃতীয়াংশ ক্যালোরির উৎস।
কেউ পুষ্টিমান বাড়ানোর কৌশল আনছেন; কেউ এমন জাত উদ্ভাবন করছেন, যা একসঙ্গে দুটি বিধ্বংসী রোগ রোধ করতে পারে—যেগুলো কাসাভা ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে।
আমাদের ফাউন্ডেশন মেকেরেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ কম্পিউটার বিজ্ঞানীর সঙ্গেও কাজ করছে—তিনি এমন মোবাইল অ্যাপ বানিয়েছেন, যাতে কৃষকরা গাছের ছবি তুলে আপলোড করলেই রোগ সংক্রমণ শনাক্ত করা যায়।
প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে—এমন উদ্ভাবকেরাই মহাদেশজুড়ে কৃষিতে রূপান্তর আনতে পারেন। বহু দশক কৃষিতে বড় বিনিয়োগ হয়নি—অনেক সরকার কৃষি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগসূত্র দেখেননি।
এখন সেই ভুলভ্রান্তি দূর হচ্ছে। ‘সমগ্র আফ্রিকান কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি’র মতো কাঠামো আছে—যার মাধ্যমে দেশগুলো কৃষি রূপান্তরের রূপরেখা পাচ্ছে। এখন বিনিয়োগ বাড়াতে হবে—যাতে তরুণ আফ্রিকানরা তাদের কল্পনার সমৃদ্ধ কৃষি গড়তে পারে।
কৃষিকে ভিত্তি করে পরের ধাপ—অন্য খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানো। এর জন্য অবকাঠামো—বিশেষ করে জ্বালানি—বিনিয়োগ দরকার।
আফ্রিকায় প্রতি দশজনের প্রায় সাতজনের বিদ্যুৎ নেই—এতে সবকিছুই কঠিন হয়ে ওঠে। অন্ধকার ক্লিনিকে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন; তীব্র গরমে ক্লাসরুমে শেখা কঠিন; শ্রমসাশ্রয়ী যন্ত্র ব্যবহার না থাকলে উৎপাদনশীলতাও কম।
পরিণতিতে—শক্তি ঘাটতি—যা বহু আফ্রিকান দেশ—দক্ষিণ আফ্রিকাসহ—ভোগ করছে—অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বড় প্রতিবন্ধক।
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ বিনিয়োগ করবে না—যেখানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা যায় না।
সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের হিসাব—২০৪০ সালেও আফ্রিকায় পাঁচশো মিলিয়ন মানুষের বিদ্যুৎ থাকবে না। এটি বদলাতে হবে।
আফ্রিকার দরকার—যা বিশ্বেরও দরকার—সবার জন্য সস্তা, পরিচ্ছন্ন শক্তির যুগান্তকারী অগ্রগতি।
গত দুই বছর আমি এ বিষয়েই প্রচুর সময় ব্যয় করেছি—কারণ এটি অত্যন্ত জরুরি। আমি এমন একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে আছি—যারা সরকারগুলোর সঙ্গে মিলে শক্তি খাতে গবেষণা-উন্নয়ন বাড়াচ্ছেন—বেসরকারি বিনিয়োগও বহুগুণ বাড়াতে কাজ করছেন।
আমার রাগ হয়—আফ্রিকা জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ ফল ভোগ করছে—যদিও এই সংকট সৃষ্টি করতে আফ্রিকানদের ভূমিকা সামান্য।
ধনী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—তাদের জ্বালানি গবেষণা বাজেট দ্বিগুণ করবে—যাতে বৈশ্বিকভাবে প্রযোজ্য যুগান্তকারী উদ্ভাবন আসে—এটা জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে।
আফ্রিকার বিদ্যুৎ এখনই দরকার। নতুন আবিষ্কারের আগেই অনেক বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।
আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ ও ভূ-তাপীয় শক্তি আছে—যা নির্ভরযোগ্য ও নবায়নযোগ্য—এসব বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। ক্ষুদ্র গ্রিড, ক্ষুদ্র-সৌর ব্যবস্থায়ও অনেক কাজ হয়েছে। এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মৌলিক চাহিদার বিদ্যুৎ মেলে—তবে বড় পরিসরের বিদ্যুৎও দরকার—সুশাসিত জাতীয় গ্রিডসহ।
এর মানে—বিদ্যুৎব্যবস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করা—বিল আদায় নিশ্চিত করা—এবং নেটওয়ার্ককে শতভাগ নির্ভরযোগ্য করা।
একবার যখন ইউটিলিটিগুলো অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে, তখন সেটাই অর্থনীতিকে টেনে তুলবে—কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এমন বিনিয়োগ সম্ভব হবে।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি উৎপাদনশীলতা, জ্বালানি ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান—এসব ক্ষেত্রেই আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বললাম—এসব অগ্রগতি সম্ভব হয় তখনই, যখন সরকারসমূহ যথেষ্ট কার্যকর।
মো ইব্রাহিমের ‘আফ্রিকান গভর্নেন্স সূচক’-এর মতো উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই—যা মহাদেশের প্রতিটি দেশে শাসন-কার্যকারিতার বহু সূচকে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে।
অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকরাও এমন একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টায় লাভবান হবেন—যা কার্যকর শাসনকে আলোকিত করে—ছড়িয়ে দেয়।
রাজস্ব শাসন ও জবাবদিহিতায় জোর দিলেও অনেক কিছু করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার বাজেট-সংক্রান্ত তথ্য জনসমক্ষে দেওয়ার জন্য ভালো নম্বর পায়।
আন্তর্জাতিক বাজেট অংশীদারিত্ব—একটি স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষক সংস্থা—সরকারি ব্যয় তদারকির ক্ষেত্রেও দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চ মূল্যায়ন করে।
কিছু দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগও দারুণ কাজ করছে। নাইজেরিয়ায় ত্রিশ বছরের অলুসেউন অনিগবিন্দে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার ছেড়ে পুরো সময় ব্যয় করছেন ফেডারেল ব্যয়ের স্বচ্ছতা আনতে।
ডেটা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি ‘বাজগিট নাইজেরিয়া’ প্রতিষ্ঠা করেছেন—যা সাধারণ নাগরিকের বোধগম্য ভাষায় তথ্য-উপাত্ত দেয়। নিঃসন্দেহে তিনি নাইজেরিয়ার কিছু প্রভাবশালীর চোখে কাঁটা—কিন্তু আমার কাছে তিনি উদাহরণ—একজন মানুষ কীভাবে পরিবর্তন আনতে পারেন।
সরকারগুলো অতীত থেকে শেখার পাশাপাশি নতুন পথও বেছে নিতে পারে। তাদের বড় সুযোগ—ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা—যাতে ব্যাংকিং ও সরকারি সেবাদানে ব্যয়বহুল পুরোনো অবকাঠামো ‘লিপফ্রগ’ করে এগোনো যায়।
মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি মানুষ ডিজিটালি অর্থ সংরক্ষণ করছেন—ফোন দিয়ে ডেবিট কার্ডের মতো লেনদেন করছেন।
কেনিয়ার ‘এম-পেসা’ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এসব সেবা কেবল অর্থ স্থানান্তরের উন্নত পদ্ধতি দেয় না—মানুষকে সঞ্চয়ের সুযোগ দেয়—যাতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু করা যায়, সন্তানের স্কুল ফি দেওয়া যায়। বন্ধু-পরিবারের অনানুষ্ঠানিক বীমা-নেটওয়ার্ক তৈরি হয়—অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সামলানো সহজ হয়। ছোট ব্যবসার লাভ বাড়ে—লেনদেন খরচ কমে—পণ্য-সরবরাহ অর্ডার করা সহজ হয়—অর্থসম্পদের নিরাপত্তা বাড়ে।
ডিজিটাল আর্থিক সংযোগ সরকারের সেবাদানকেও দক্ষ করে। ভারতের গবেষণা বলছে—পরিবারগুলোকে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমে সংযুক্ত করে ও সরকারের সব পেমেন্ট স্বয়ংক্রিয় করে বছরে কয়েক দশ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় সম্ভব।
আফ্রিকায়ও প্রাথমিক প্রমাণ বলছে—এমন প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য সুফল দিতে পারে। যেমন—উগান্ডায় সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে—খাবার হিসেবে সরাসরি সহায়তার বদলে ডিজিটাল নগদ হস্তান্তর করলে শুধু বিতরণ খরচই কমে না—পুষ্টিও উন্নত হয়—কারণ মানুষ টাকা দিয়ে বৈচিত্র্যময় খাবার কিনতে পারে—প্রয়োজনমতো খাবারের সময়ও ঠিক করতে পারে।

বেসরকারি বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও সুস্থ প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করে এমন নীতিমালা করে সরকারগুলো এই ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করতে পারে।
কেনিয়া, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া—এ ধরনের দেশগুলো ইতিমধ্যেই নতুন ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্মের ভিত্তি নির্মাণে বিনিয়োগ করছে—আমার বিশ্বাস, তারা বড় ধরনের ইতিবাচক ফল পাবে।
একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত—আফ্রিকা তার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ অর্জন করতে পারে।
সেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—আফ্রিকার মানুষ অর্থনৈতিক-সামাজিক স্তর ও জাতীয় সীমানা পেরিয়ে একসঙ্গে কাজ করবেন কি না—এমন এক ভিত্তি গড়ে তুলতে—যাতে আফ্রিকার তরুণরা প্রাপ্য সুযোগ পায়।
সম্প্রতি আমার আদ্দিস আবাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাদের সেই ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করি—যা আপনি আমেরিকান কলেজ শিক্ষার্থীদের করেন—“স্নাতক শেষে কী করতে চাও? কোন ক্ষেত্রে যেতে চাও?”
তারা আমাকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে—কারণ প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত। তারা মনে করে—তাদের বাবা-মা দশকের পর দশক ত্যাগ স্বীকার করেছেন—যেন তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে। তারা ‘বিকল্প’ ভাবছে না—নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে—সেটি কাজে লাগিয়ে দেশকে আরও সমৃদ্ধ করতে তারা উদগ্রীব।
তারা নিজেদের বৃহৎ এক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে দেখে—যার বিশাল প্রয়োজন আছে—আর সেই প্রয়োজন মেটাতে নিজেদের উৎসর্গ করতে চায়।
আফ্রিকায় এলেই—বিশেষ করে তরুণদের সঙ্গে কথা বললেই—আমি এই উদ্দেশ্যচেতনাকে দেখি। আমার মনে হয় এটি এক অনন্য সম্পদ—মানুষ পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে—ফিরিয়ে দিতে চায়।
এখানকার শিক্ষার্থীরা শুধু নিজেদের প্রতি নয়—নিজেদের দেশ ও মহাদেশের ভবিষ্যতের প্রতিও বিশ্বাসী। আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত—তাদের সেই বিশ্বাসকে কাজে রূপ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া—কারণ এমন উদ্দেশ্যপ্রবণ তরুণরাই স্থবিরতা আর দ্রুত অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।
নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, “তরুণরা যদি জেগে ওঠে, তাহলে তারা অত্যাচারের টাওয়ার ভেঙে স্বাধীনতার পতাকা তুলতে সক্ষম।” কিন্তু আমাদের দায় কেবল জাগিয়ে তোলায় শেষ নয়—আমাদের দায় তাদের ওপর বিনিয়োগ করা—মৌলিক অবকাঠামো গড়ে দেওয়া—যাতে তারা ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।
আর আমাদের তা এখনই করতে হবে—কারণ আগামীকালের উদ্ভাবন নির্ভর করে আজকের শিশুদের সুযোগের ওপর।
হয়তো পরিষ্কার—এগুলো বড় ও জটিল চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ততটাই স্পষ্ট—সাহস, শক্তি, বুদ্ধি, আবেগ ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানুষ বড় ও জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে—আর সেগুলো জয় করতে পারে।
আমাদের ‘একসঙ্গে বসবাস’-এর ভবিষ্যৎ গড়তে অনেক কাজ বাকি—কিন্তু ততটাই মানুষ প্রস্তুত—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব।
চলুন, আমাদের সাধ্যের সবটুকু এখনই করি—নেলসন ম্যান্ডেলার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়তে—এবং সেই ভবিষ্যৎ আমরা একসঙ্গে অর্জন করব।
ধন্যবাদ।

 সারাক্ষণ রিপোর্ট
সারাক্ষণ রিপোর্ট