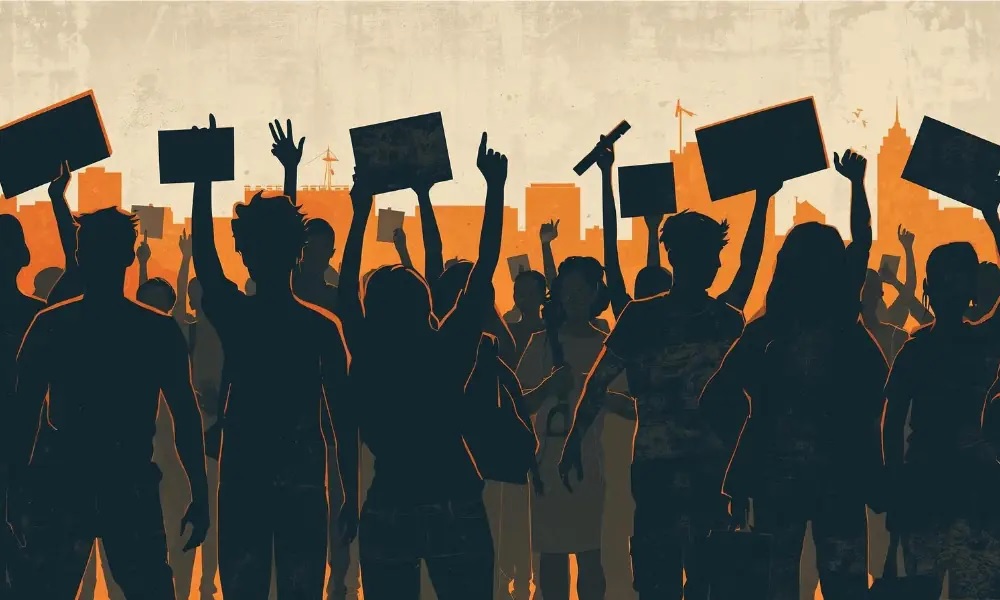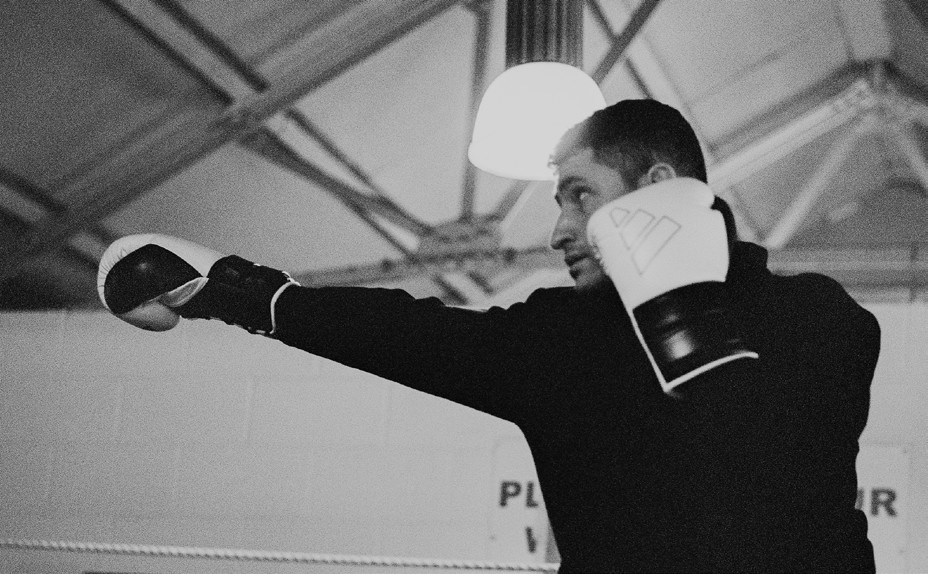তরুণরা দেখিয়েছে—তারা শাসনব্যবস্থাকে নেড়ে দিতে পারে। কিন্তু সংগঠন, আদর্শ ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের পথনির্দেশ ছাড়া তাদের ক্রোধ শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান স্থিতাবস্থাকেই আরও পোক্ত করে।
২০১১ সালে তিউনিসিয়ায় এক শিক্ষিত পথফেরিওয়ালার আত্মাহুতি থেকে সূচনা হয় সুবিখ্যাত ‘আরব বসন্ত’। তা মিসর, বাহরাইনসহ বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দশকের পর দশক লৌহমুষ্টি দিয়ে শাসন করা একনায়ক ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।
জনতা কিছু জয়ও পেয়েছিল—জিন এল আবিদিন বেন আলি ও হোসনি মুবারকের মতো ঘৃণিত শাসকদের হটানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরব বসন্ত তেতো স্বাদই রেখে গেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রায় সব দেশেই কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং আরও শোষণমুখী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিরিয়া ও লিবিয়ার মতো দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী মদদে প্রক্সি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রায় ১৫ বছর পর দেখা যাচ্ছে—স্থিতাবস্থা শুধু ফিরে আসেনি, বরং আরও দৃঢ় হয়েছে।
সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে নেপালে যে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেশটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তা পাকিস্তানেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়; কেউ কেউ আরব বসন্তের সঙ্গে তুলনাও টেনে আনেন। শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সঙ্গে নেপালের ঘটনাকে মিলিয়ে অনেকে বললেন—দক্ষিণ এশিয়াই নাকি নতুন মধ্যপ্রাচ্য।
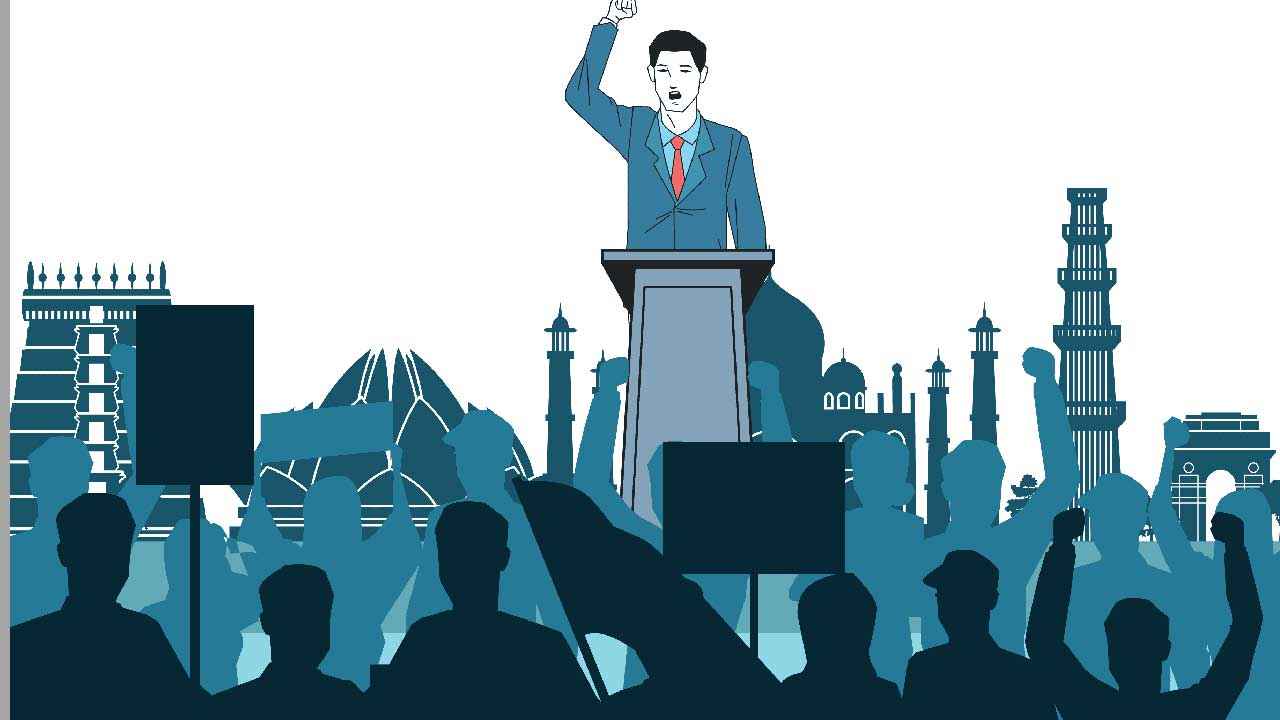
আসলে এক নতুন স্বাভাবিকতা তৈরি হয়েছে—যেখানে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত তরুণ জনগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করছে। তবে প্রশ্ন হলো, এই নতুন রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গির শেষটা কোথায় গিয়ে ঠেকে?
এর উত্তর খুঁজতে গেলে সাম্প্রতিক বছরগুলোর দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অভ্যুত্থানের মিল-অমিল টেনে দেখা দরকার; একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের অন্যত্র ঘটে যাওয়া অনুরূপ আন্দোলনের পাশে এদের বসাতে হবে। পাকিস্তান ও তার প্রতিবেশীরা এই বৈশ্বিক প্রবণতাকে আরও জোরদার করবে, নাকি নিজেদের পথ রচবে—তা সময় বলবে। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত—‘তরুণ জনসংখ্যার ঢেউ’র রাজনীতি এখানেই থাকতে এসেছে।
অর্থনীতিই মুখ্য
আরব বিশ্বের বহু অঞ্চলের মতোই আমাদের অঞ্চলেও সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতিক দুর্দশা। নেপালে সরকার যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করল—যে প্ল্যাটফর্মগুলো তরুণদের কাছে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জায়গা, আবার অত্যন্ত অনিশ্চিত গিগ-ওয়ার্কেরও অবলম্বন—তখন তরুণরা রাস্তায় নেমে পড়ে। ধারাবাহিক বামঘেঁষা সরকারগুলো পর্যাপ্ত জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে; বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব মিলিয়ে হার ২০ শতাংশেরও বেশি বলে ধরা হয়। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই—অসংখ্য নেপালি বিদেশে কাজ খোঁজেন; রেমিট্যান্স এখন দেশের জিডিপির প্রায় ৩৩ শতাংশ।
অঞ্চলজুড়েই চিত্রটা মোটামুটি একই; আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে জনসংখ্যা আরও তরুণ, আর বিদেশে কর্মরত অভিবাসীর সংখ্যা কোটির ঘরে। উল্লেখযোগ্য অংশ মানবপাচারকারীদের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে মৃত্যুসহ ভয়াবহ পরিণতির মুখে পড়েন। সংকটের শেকড়ে আছে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের কোনো স্থায়ী কর্মসূচির অনুপস্থিতি—যা দ্রুত সম্প্রসারিত শ্রমশক্তিকে শোষণ করতে পারে; বিশেষত কৃষি খাত থেকে যাদের ক্রমে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। যারা বিদেশ যেতে পারেন না, তাদের বিপুল অংশ ঠাঁই নেন অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে—সুপারশোষণ, অনিশ্চয়তা আর ভবিষ্যৎহীনতার মধ্যে। নেপালের উদাহরণই দেখায়—তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত তরুণরাও সাময়িক, স্বল্প-মজুরির গিগ-ওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল—যা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অনিশ্চয়তার একসঙ্গে প্রতীক।

মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—পুঁজির দ্বারা মজুরিশ্রমের অর্থনৈতিক শ্বাসরোধ এমন এক বস্তুগত পরিস্থিতি ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে, যা আদর্শগত কর্মসূচিতে সজ্জিত হলে শ্রমিক গণকে বিপ্লবে উসকে দিতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার তরুণরা নিয়মিত মজুরির কাজই পান না; উপরন্তু কোনো সঙ্ঘবদ্ধ আদর্শগত ঐক্য ও সংগঠন ছাড়া তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মযজ্ঞ এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা মধ্যস্থ।
ডিজিটাল জীবজগৎ
পাকিস্তানের সীমানা ছাড়িয়েই বোঝা যায়—ডিজিটালায়ন রাজনীতিকে কতখানি বদলে দিয়েছে। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)–এর মতো মূলধারার দল, তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)–এর মতো ধর্মভিত্তিক সংগঠন, আওরাত মার্চের নারীবাদী উচ্চারণ, কিংবা বালুচ ইয়েকজেহতি কমিটি (বিওয়াইসি) ও নিষিদ্ধ পশতুন তাহাফ্ফুজ মুভমেন্ট (পিটিএম)–এর মতো জাতিগত প্রান্তের জনপ্রিয় আন্দোলন—সব ক্ষেত্রেই তরুণরা প্রধানত অনুপ্রাণিত হয় এবং সংগঠিতও হয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে।
পাশাপাশি রাষ্ট্রও তার ক্ষমতা এবং বিগ টেক প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে আঁতাত—দুটো দিয়েই ডিজিটাল জীবজগতের আদর্শিক পরিসরকে সঙ্কুচিত করে; জনপ্রিয় আন্দোলনের দাবিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এমনকি অপরাধীও বানিয়ে ফেলে। উপরের উদাহরণগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে একমাত্র টিএলপি-ই এমন আক্রমণ থেকে তুলনামূলক রেহাই পেয়েছে।
যত বেশি তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হচ্ছে, অনলাইন কনটেন্টে ততই রাজনৈতিক রং ঘন হচ্ছে—বিদ্রূপ-ব্যঙ্গও বাড়ছে। যারা অনলাইনে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়, তাদের বড় অংশই বোঝে না—তাদের ডেটা বিগ টেক ব্যবহার করছে রাষ্ট্রের নজরদারিকে সুবিধা দিতে; আর সমালোচনামূলক গবেষকের ভাষায় ‘প্ল্যাটফর্ম পুঁজিবাদ’-এর ব্যবসায়িক মডেলই দাঁড়িয়ে আছে ব্যবহারকারীদের ডেটা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বেচে দেওয়ার ওপর।
এই অর্থে তরুণদের কাছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মই প্রায় একমাত্র জায়গা, যেখানে তারা গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিষ্ঠানসমর্থিত ও সম্পদশালীদের নিয়ন্ত্রণে; মূলধারার সংবাদমাধ্যমও চলে ‘নির্দিষ্ট সীমা’র ভেতরে। তাই জনপ্রিয় আন্দোলনগুলোর বড় অংশই ডিজিটাল পরিসরে জন্ম নেয়।

তবু সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট। আরব বসন্তের বহুল প্রশংসিত ‘আড়াআড়ি’ বা লিডারবিহীন চরিত্র শেষ পর্যন্ত ভাঙনের পথে গেছে, আর রাষ্ট্র ও শ্রেণিশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আর এখন নেপাল—সবখানেই শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রই ‘শূন্যতা’ পূরণে সামনে এসেছে।
নেপালে ২০০৫ সালে অপসারিত রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে প্রোরয়্যালিস্টদের পুনরুত্থান ঘটেছে। ফলত কমিউনিস্ট বামদের ঐতিহাসিক অর্জন—সশস্ত্র সংগ্রাম সফল করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা—বেশির ভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত। তারা না তৃণমূলে টেকসই রাজনৈতিক সংগঠন গড়তে পেরেছে, না রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে রূপান্তরমুখী অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। ফল হলো—বঞ্চিত তরুণ গণসমুদ্র, যারা ডিজিটাল সমাবেশ কৌশলে ভর করে স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিবাদের বিস্ফোরণ ঘটায়।
পাকিস্তানের বেলায় পিটিআই মূলত অনলাইনে লক্ষ লক্ষ তরুণকে সংগঠিত করেই উত্থান ঘটায়। যে কুখ্যাত সময়ে দলীয় নেতৃত্ব ও সামরিক স্থাপনা ‘একই পাতায়’ ছিল, তখন এই অনলাইন সমর্থনভাগই তথাকথিত ‘পঞ্চম প্রজন্মের যোদ্ধা’র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রথম সারি হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু ২০২২ সালের এপ্রিলে যখন ইমরান খানের সরকার প্রায় আক্ষরিক অর্থেই ক্ষমতা থেকে ‘বুট’ খেয়ে বেরিয়ে গেল, তখন অনলাইন জনমত উল্টো দিকে ঘুরল। তিন বছরেরও বেশি কেটে গেছে—তবু স্পষ্ট যে পিটিআইয়ের ভয়ংকর ডিজিটাল পৌঁছের পরও মাঠের সংগঠন এতটাই পাতলা যে জবরদস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী দমন-পীড়ন সামলাতে পারছে না।
‘রঙিন বিপ্লব’ থেকে সাবধান
‘রঙিন বিপ্লব’ কথাটি সবচেয়ে জোরালোভাবে যুক্ত পূর্ব ইউরোপে ‘বাস্তব সমাজতন্ত্র’-এর পতনের সাথে জুড়ে আছে। ইউক্রেন থেকে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া—১৯৮০–এর দশকের শেষভাগ থেকে যে ঢেউ উঠল, তাতে ভেসে এল ‘উদার’ গণতন্ত্র ও তথাকথিত ‘মুক্তবাজার’ অর্থনীতি। বাস্তবে এসব রঙিন ‘বিপ্লব’ প্রো-পশ্চিম শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়েছে; তারা সরকারি সম্পদের ‘অগ্নিবিক্রি’ধরনের বেসরকারিকরণ করেছে এবং নতুন এক দমনমূলক অলিগারকি কায়েম করেছে।
পরে দেখা গেল, আরব বসন্তও অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ ও তার নানা অনুসারীর দ্বারা কব্জা হয়েছে। তিউনিসিয়ার আন্দোলনকে পশ্চিমা গণমাধ্যম ‘জ্যাসমিন বিপ্লব’ নামও দিয়েছিল—যা দেশের ভেতরেই অনেকেই তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এতে তাদের সংগ্রামের ওপর বাইরের এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ধরে না নিলেও বোঝা যায়—বাংলাদেশে ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনটি দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তির ভারসাম্য এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক—দুই দিকেই বড় প্রভাব ফেলেছে। মুহাম্মদ ইউনুসের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, সেনা-উচ্চপদস্থদের ও ধর্মীয় ডানপন্থার পুনরুজ্জীবন—সবই ইঙ্গিত দেয়, তরুণদের আকাঙ্ক্ষা পুরোনো শাসকগোষ্ঠী দ্বারা মধ্যস্থ হচ্ছে। যেখানে শেখ হাসিনার আমলে ঢাকা-নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠতা প্রকট ছিল, বর্তমান বাংলাদেশি ব্যবস্থায় রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদের জন্য বেশি পরিসর তৈরি হয়েছে।
নেপালে বিক্ষোভ চলাকালীনই বিশেষ সহিংস উপাদান নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়—যারা কৌশলগতভাবে অগ্নিসংযোগে নেমেছিল; সাবেক এক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী রাবিলক্ষ্মী চিত্রকার গুরুতর দগ্ধ হয়ে এখনও সংকটাপন্ন। এরপর কিছু জেন জেড ছাত্রনেতা বলেছেন—তাদের পুরো আন্দোলনটাই ‘হাইজ্যাক’ হয়ে গেছে; ধুলো থিতিয়ে গেলে ‘সংস্কার’ এজেন্ডা চাপাতে সেনাবাহিনী যে কাউকে ‘দাঙ্গাবাজ’ বলে চিহ্নিত করে নির্মূল করতে পারে—এমন অবস্থানেই তারা পৌঁছেছে।
আদর্শগত ঐক্য কোথায়?
নৈরাশ্যবাদে না গিয়ে—যেখানে জনতার সব রাজনৈতিক উত্থানই নাকি শেষত পরাজিত হবে—একটি মৌলিক সত্য স্বীকার করা জরুরি: জনগণের ইচ্ছাশক্তি টিকে থাকে তখনই, যখন তা শক্তিশালী, তৃণমূলে প্রোথিত রাজনৈতিক বাহনে প্রবাহিত হয়—যা পুরোনো শাসকগোষ্ঠীর কাছে বন্ধকী নয়।
‘তরুণ জনসংখ্যার ঢেউ’র রাজনীতি হলো ঔপনিবেশ-পরবর্তী পুঁজিবাদের অন্তর্গত পচনের প্রতিচ্ছবি—যা এখন সম্মতির ভানও ছাড়ছে, শিক্ষিত তরুণ অংশকেও বিচ্ছিন্ন করছে। শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও বিদেশি অভিভাবকেরা ক্রমে বেশি ভর দিচ্ছে দমন-পীড়ন ও/অথবা সহঅপশন কৌশলে। মূলধারার দলগুলো বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি বলতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। এ কারণেই তরুণ শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এখন ডিজিটাল ক্ষোভে আশ্রয় নিচ্ছে।
কিন্তু এটি তাদের অস্তিত্বের শর্ত বদলাতে যথেষ্ট নয়। বরং সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী দিগন্ত আর সমপর্যায়ের সাংগঠনিক সক্ষমতা ছাড়া—উত্থানের উল্লাস বেশির ভাগ সময়ই পরিণত হয় হতাশায়, এবং বিদ্যমান স্থিতাবস্থা আরও গভীরতর হয়।
(লেখাটি ডন থেকে অনূদিত)

 আসিম সাজ্জাদ আখতার
আসিম সাজ্জাদ আখতার